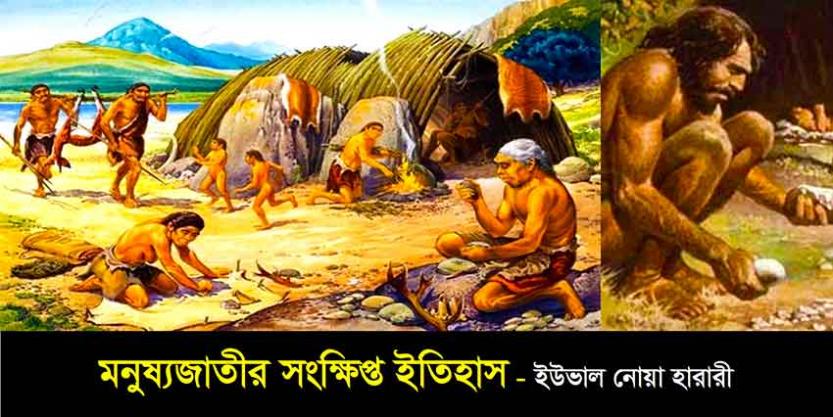
মনুষ্য জাতীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । ইউভাল নোয়া হারারী
বঙ্গানুবাদ- আশফাক আহমেদ
আপনার হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ কি বিয়ের এতো বছর পরেও অন্য নারী/পুরুষ দেখলেই ছোঁক ছোঁক করেন? আপনারা বাবার কি ডায়বেটিক? হাজার বার মানা করা সত্ত্বেও উনি কি মিষ্টি জাতীয় খাবারের লোভ সামলাতে পারেন না? কিন্তু কেনো এই ঘটনাগুলো ঘটছে? কে দায়ী এইসবের পেছনে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আসলে আমাদের আশেপাশে তাকিয়ে পাওয়া যাবে না। এর উত্তর পেতে হলে আমাদের একটু পেছনে ফিরতে হবে। বেশি পেছনে না। মাত্র ৩০ হাজার বছর আগে। যখন আমরা শিকার আর ফলমূল সংগ্রহ করে বেঁচে ছিলাম। আমাদের সেই আদিপুরুষদের মনস্তত্ত্ব ঘাঁটলেই আমাদের আজকের মনস্তত্ত্বের কিছুটা আঁচ পাওয়া যাবে। প্রথমেই আপনার বাবার সমস্যাটা সল্ভ করি। কথা হল, মিষ্টি জাতীয় খাবারের প্রতি আপনার বাবার এতো আকর্ষণ কেনো? এই আকর্ষণ কি তার বাবা, তার বাবা এবং তার বাবারও ছিল? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ, ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো, তাদের খাবারের স্টক ছিল সীমিত। হাই ক্যালরি ফুড তো ছিল না বললেই চলে। অথচ শিকারের জন্য তো হাই ক্যালরি ফুডের দরকার। আর এই হাই ক্যালরি ফুডের একমাত্র উৎস ছিল পাকা ফলমূল। বনেজঙ্গলে তাও ছিল দুষ্কর। আমাদের গ্রেট গ্রেট দাদী- নানীরা তাই যখনই কোন পাকা ফলের সন্ধান পেতেন, অমনি ধরে তা গাপুস গুপুস খেয়ে ফেলতেন। যেন স্থানীয় বদমাইশ বেবুনের দল এর সন্ধান পাবার আগেই তারা সব ক্যালরি শরীরস্থ করে ফেলতে পারেন। বেবুনের দল মারা খাক। এই করে করে আমাদের মস্তিষ্কে মিষ্টি জাতীয় খাবারে আসক্তির একটা সার্কিট তৈরি হয়ে গেছে। আজ হয়তো আমরা হাইরাইজ এ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করি। স্মার্টফোন চালাই, গাড়ি ড্রাইভ করি। সেটা আমরা জানি, আমাদের ডিএনএ তো আর জানে না। সে ভাবে, আমরা বুঝি এখনো সেই সাভানার জঙ্গলে বসবাস করছি। কাজেই, মিষ্টি খাবার দেখলে আমাদের আর মাথা ঠিক থাকে না।
এবার আসি নারী-পুরুষ, প্রেম-ভালবাসা ঘটিত সমস্যায়। এর মূলেও আছে আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপ। মনে করা হয়, সেসময়কার সমাজে কোন ব্যক্তিগত সম্পদের কোন ধারণা ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল না বলে একগামী কোন রিলেশনেরও প্রয়োজন দেখা দেয়নি সেই সময়। যতো যাই বলেন, মানুষ কিন্তু একগামী রিলেশনে আবদ্ধ হয় এবং টিকিয়ে রাখে তার সন্তানদের কথা ভেবে, নিজেদের কথা ভেবে না। আমার সন্তান যেহেতু আমার সম্পদ পাচ্ছে না, কাজেই আমার তো একগামী (হোক না লোক দেখানো) রিলেশনে থাকারও প্রয়োজন নাই— ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম। তো নারী-পুরুষ তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে একটা ছোটখাটো দল আকারে থাকতো। এক নারী যতো খুশি পুরুষের সাথে সুসম্পর্ক (ইউ নো, হোয়াট আই মীন বাই সুসম্পর্ক) তৈরি করতে পারতো। ‘ফাদারহুড’ বলে কোন ধারণা তখনো চালু হয়নি। পুরুষ ছিল নারীদের কাছে এক রকমের সেক্স টয়। প্রকৃতি সন্তান চায়। সেই সন্তান উৎপাদনের জন্য নারী সেই সময় পুরুষকে জাস্ট ব্যবহার করতো। আর একজন ভালো মা সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই বহু পুরুষের সাথে মিলিত হতেন। যেন তার সন্তান একই সাথে দক্ষ যোদ্ধা, ভালো গল্পকার এবং প্যাশনেট প্রেমিক হতে পারে। কোন এক পুরুষের মধ্যে এই সব গুণাবলীর সম্মিলন পাওয়া দুঃসাধ্য। কাজেই, একজনের সাথে প্রেম করাটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তারপর সেই সন্তানদের দেখভাল করতো দলের সবাই মিলে। কোন পুরুষই জানতো না, ঠিক কোনটা তার সন্তান। কাজেই, সব শিশুকেই সমান চোখে দেখা হত। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোও ঠিক এরকম একটা সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। জন্মের পরপরই শিশুদের দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র। মা-বাবার উপর কোন দায়িত্ব থাকবে না। সেই শিশুরা রাষ্ট্রীয় সদনে সমান সুযোগ-সুবিধায় বড় হবে। কেউ জানবে না, তার বাবা-মা কে। বাবা-মা’রাও জানবে না, তাদের সন্তান কোনটি। একটা নির্দিষ্ট এইজ গ্যাপের সবাইকেই সেই শিশুটি বড় হয়ে বাবা বা মা ডাকবে। ব্যাপারটা অবাস্তব শোনালেও প্লেটো সম্ভবত সমাজে বিদ্যমান পাহাড়সম শ্রেণীবৈষম্য রোধে এরকম একটা ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন। ওয়েল, এমন সমাজ যে একেবারেই নেই, তা কিন্তু আমরা বলতে পারবো না। আমাদের দূর সম্পর্কের ভাই শিম্পাঞ্জী ও বোনোবোদের মধ্যে তো বটেই, আজকের যুগেও বারি ইন্ডিয়ান নামক এক ন্গোষ্ঠীর মধ্যে এরকম কালেক্টিভ ফাদারহুডের চর্চা চালু আছে। এরা বিশ্বাস করে, কেবল এক পুরুষের স্পার্ম থেকেই সন্তানের জন্ম হয় না। বহু পুরুষের স্পার্ম এক নারীর গর্ভে পুঞ্জীভূত হয়ে তবেই সন্তানের জন্ম হয়। প্রাচীন মানুষ যে সব দিক দিয়ে ভুল ছিল—তা কিন্তু না। তাদের এইসব আপাত আজগুবি ধারণার মধ্যেও কিছু কিছু সত্যতা পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখে গেছে, কোন নারী যদি বিয়ের আগে এক বা একাধিক পুরুষের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করে থাকেন, তবে তার সন্তানের মধ্যে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে। ব্যাপারটা খারাপ না, কী বলেন? একই মানুষের মধ্যে একিলিস থাকবে, হোমার থাকবে, আবার রোমিও-ও থাকবে। যাই হোক, সোজা কথা, মনোগ্যামী আসলে আমাদের রক্তে নেই। আমাদের রক্তে প্রবল উল্লাসে বয়ে চলেছে পলিগ্যামীর স্রোত। এটা নারী-পুরুষ সবার জন্যই সত্য। আর এজন্যই ভালোবেসে বিয়ে করার পরও আমাদের মধ্যে এতো ঝগড়া, এতো অশান্তি। আমাদের জিনে জিনে যে বহুগামীতার রাজত্ব। অথচ আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ আমাদের উৎসাহিত করছে একগামী হতে। ভালোবেসে, সুখে শান্তিতে বসবাস করে সৎ, চরিত্রবান স্বামী/স্ত্রীর খেতাব পেতে। আমাদের মধ্যে যে ডিপ্রেশন, যে একাকীত্ব আর নিঃসঙ্গতা, তার কারণ বোধ হয় সেই দলবদ্ধ জীবন যাপন ছেড়ে জোর করে একগামী হবার চেষ্টা করা। প্রশ্ন হচ্ছে—নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিগুলো এখনো তাহলে টিকে আছে কীভাবে? পরকীয়ার প্রভাবে তো সব উড়ে যাওয়ার কথা। এই ব্যাপারে আরেক দল মনস্তাত্ত্বিকের অন্যরকম থিওরি আছে। তারা বলেন, মানুষ স্বভাবতই মনোগ্যামাস এবং তার পার্টনারের ব্যাপারে পজেসিভ। অন্তত আমাদের ভাই- বেরাদরের তুলনায় আমরা অনেক বেশি মনোগ্যামাস। বাইরে আপনি যতোই প্রগতিশীল ভাব দেখান না কেনো, আপনার বউ/গার্লফ্রেন্ড আরেকজন পটেনশিয়াল পুরুষের গায়ে ঢলে পড়ে হেসে হেসে কথা বললে আপনার মধ্যে একটু হলেও খচখচ করবে। ব্যাপারটা মেয়েদের জন্যেও সত্য। এই থিওরিস্টরা বলেন, প্রাচীন সমাজেও এরকম একটা ব্যাপার ছিল। এরা দল বেঁধে থাকলেও যাকে বলে ‘ফ্রি সেক্স’ তা এদের মধ্যে ছিল না। কাপলরা নিজেদের মত করে থাকতো। নিজেদের বাচ্চা নিজেরাই সামলাতো। বিপদে- আপদে পড়লে কেবল দলের অন্যদের সাহায্য নিত। নিজেদের সন্তানের প্রতি আমাদের যে এক ধরনের অন্ধত্ব কাজ করে, সে কাউকে খুন করে আসলেও মা যে তাকে ফেলে দিতে পারেনা না—এই ব্যাপারটা তখন থেকেই আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে।
পার্টনারের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই। আপনি হয়তো সবার কাছে আপনার পার্টনারের হাজারটা বদনাম করে বেড়ান। কিন্তু অন্য কেউ আপনার পার্টনারকে সামান্য সময়ের জন্যও দখল করতে এলেও ঠিকই আবার বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ান। এই যে পজেসিভনেস, এইটা আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই আমাদের রক্তে বাহিত হয়ে আসছে। অনেকে বলেন, আজকের প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে বিয়ে টিকে থাকার কথা না। এখনো যে টিকে আছে, তার কারণ বোধয় বহু বছরের এই অভ্যাস। নেক্সট টাইম আপনার পার্টনার যদি আপনাকে নিয়ে একটু পজেসিভ হয়ও, তাকে ভুল বুঝবেন না প্লিজ। সবই আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপের ফসল। শারীরিক দিক দিয়ে তো বটেই, স্রেফ মগজের দিক দিয়েও আমাদের শিকারী পূর্বপুরুষেরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে ছিল। অন্তত তথ্য প্রমাণ তাই বলে। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য, গত তিরিশ হাজার বছরে আমাদের মগজের তেমন উন্নতি হয়নি। বরং কিছুটা অবনতি হয়েছে বলা যায়। তাহলে এই যে আমাদের আধুনিক সভ্যতা, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, স্পেসশিপ—এগুলো কার অবদান? কোন ভিনগ্রহী এসে তো এগুলো তৈরি করে দিয়ে যায়নি। এগুলো আমাদের মগজেরই অবদান। সত্যি করে বললে, আমাদের কালেক্টিভ মগজের। ইনডিভিজুয়াল মগজের সাইজ সত্যিই কমেছে। প্রাচীন মানুষ ছিল ভয়াবহ লেভেলের জ্ঞানী। সারভাইভালের জন্যই তাদের জ্ঞানী না হয়ে উপায় ছিল না। আজ একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার জগৎ-সংসার, পাড়া- প্রতিবেশী সম্বন্ধে কিছু না জেনেই দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। প্রাচীন মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না। নিজেদের এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি সম্বন্ধে তাদের নিখুঁত জ্ঞান রাখতে হত। আমরা যেখানে গুগল ম্যাপ ছাড়া পাশের গলিতে ওয়ালমার্ট আছে কিনা, তাও বলতে পারি না। খাবার সংগ্রহের কথাই ধরা যাক না কেন। কোন ফল কখন হয়, সেই জ্ঞান তো তাদের ছিলই, প্রতিবেশী বানর কিংবা হনুমানের দল এগজ্যাক্টলি কখন সেই ফলে আক্রমণ করে বসবে, সেই জ্ঞানও তাদের রাখতে হত। এইখানেই শেষ নয়। কোন ফল খেতে মজা, কোন ফলে বিষ আছে আর কোন ফল রোগবালাইয়ে ওষুধের কাজ দিবে—এই সব তাদের নখদর্পণে ছিল। এগুলো ছিল সেকালের সাধারণ জ্ঞান। প্রত্যেক ইনডিভিজুয়ালকে এই জ্ঞানটুকু রাখতে হত। কোন ডাক্তার- বৈদ্য যেহেতু ছিল না তাদের বলে দেবার জন্য কিংবা লিখিত ভাষাও চালু হয়নি যে ফলের গায়ে কোন নিঃস্বার্থ মানুষ এসে লিখে রাখবেঃ “সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণঃ এই ফলে বিষ আছে। এই ফল খাবেন না।” পশু শিকারের জন্য তাদের প্রয়োজন হত হাতিয়ার। এই হাতিয়ারও ছিল হিজ হিজ হুজ হুজ। সেই সময় মানুষ তাই ব্যবহার করতো, যা সে নিজে তৈরি করতো। ধরা যাক দুই একটা হারপুন এবার। যে লোকটা হারপুন বানাতো, সেই ঐ হারপুন দিয়ে শিকার করতো। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ব্যবহার্যই তাই। ফলে কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে গোটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের খুঁটিনাটি সে জানতো। আর ভালো শিকারের জন্য দরকার ভালো হারপুন। নিজের হারপুনকে সেরা শেপটা দেবার জন্য তাকে মগজ খাটাতেই হত। আজ তার কুলাঙ্গার বংশধর কম্পিউটার ব্যবহার করে, সে কিন্তু জানে না, কম্পিউটার কীভাবে তৈরি হয়। কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে–এটাও সে জানে না। অথচ সে মনের আনন্দে কম্পিউটারে চ্যাট করে চলেছে। এর নামই টেকনোলজি। যা আমাদের মাথা না খাটিয়ে সুবিধাটুকু পুরোপুরি উপভোগ করার সুযোগ এনে দেয়, তাই টেকনোলজি।
ক্যালকুলাস যেমন গণিতের একটা শাখা। কিন্তু ক্যালকুলাসের সুত্রগুলো আপনি না বুঝেও আপনার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। sinX কে ডিফারেনশিয়েট করলে cosX পাওয়া যায়। এটা আমরা সবাই জানি। কীভাবে পাওয়া যায়া—এটা না বুঝলেও কিন্তু আপনি পরীক্ষার খাতায় নম্বর পেয়ে যাচ্ছেন কিংবা ফিজিক্সের একটা থিওরি প্রমাণ করতে কাজে লাগাতে পারছেন। এই ক্ষেত্রে ক্যালকুলাস কিন্তু গণিত বা বিজ্ঞান নয়, ক্যালকুলাস একটা প্রযুক্তি। প্রাচীন মানুষের কাছে হাতিয়ার ছিল, কিন্তু সেই অর্থে টেকনোলজি ছিল না। পেশাভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস তখনো তৈরি হয় নি যে কোন একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার দলের সব হারপুন তৈরি করবে। বাকি সবাই তা নিয়ে শিকারে বেরোবে। কাজেই, এখন আমরা একটা বস্তুর ফিজিক্স নিয়ে যতো গভীরভাবে চিন্তা করি, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তার চেয়েও বেশি চিন্তা করতেন। চিন্তা করতে বাধ্য হতেন বলা যায়। ফলে, তাদের মগজের ব্যবহারও ছিল বেশি। আমরা যে দিন দিন আমাদের মগজের ব্যবহার কমিয়ে দিচ্ছি, তা নিয়ে কখনো ভেবেছি কি? লাইফস্টাইলের দিক দিয়েও তারা আমাদের চেয়ে যোজন যোজন এগিয়ে ছিলেন। আজ একজন কর্পোরেট মানুষের ঘুম ভাঙে সকাল সাতটায়। কোনোভাবে নাশতা করে তাকে অফিসের উদ্দেশ্যে দৌড়াতে হয়। তারপর আট কি দশ ঘণ্টা অমানুষিক খাটা খেটে রাতে বাসায় ফিরে আর কিছু করার এনার্জি থাকে না আসলে। তা বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলাই হোক কিংবা স্ত্রীর সাথে।
অথচ ত্রিশ হাজার বছর আগে সেই একই মানুষটি সকাল নয়টা কি দশটায় হেলেদুলে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে বের হত। ফলমুল, মাশরুম সংগ্রহ করে দিন কাটাতো। মাঝেমধ্যে ভুল করে বাঘ মামার টেরিটোরিতে ঢুকে পড়েই আবার দৌড়ে পালাতো। চারটার দিকে বাসায় ফিরে পরিবারের সবাই মিলে রান্নাবান্না করতো। বাচ্চাদের সাথে খেলতো। বাঘ মামার হাত থেকে বেঁচে আসার গল্প শোনাতো। সপ্তাহে পাঁচদিন বা ছয়দিন যে সে এই রুটিন ফলো করতো —তাও নয়। বড়জোর দুই কি তিন দিন। অনেক সময় ভালো একটা শিকার পেলে গোটা সপ্তাহই পায়ের উপর পা তুলে কাটিয়ে দিত। কাজেই, হ্যাংআউট করার জন্য তাদের হাতে ছিল অফুরন্ত সময়। আজ আমাদের হ্যাঙ্গাউট করার জন্য কতো প্ল্যান-প্রোগ্রাম করতে হয়। নিজের স্কেজিউল দেখতে হয়। বসের স্কেজিউল দেখতে হয়। তাদের এইসব স্কেজিউল দেখার প্যারা ছিল না। পরিবারের সবাই মিলে যখন খুশি যেখানে খুশি হ্যাং আউট করতে যেত। আগে থেকে বুকিং করারও ঝামেলা ছিল না। দুর্ভিক্ষ বা অপুষ্টি কাকে বলে—তারা জানতো না। দুর্ভিক্ষ তো কৃষিযুগের স্ষ্টি আর অপুষ্টি আধুনিক শিল্পযুগের। তাদের গড় আয়ু হয়তো খুব বেশি ছিল না। তিরিশ কি চল্লিশ বছর। তার কারণ অধিক শিশু মৃত্যুহার। কিন্তু যারা অল্প বয়সে সারভাইভ করে যেতো, তারা ঠিকই বছর ষাটেক সুস্থ সবল বেঁচে থাকতো। তাদের এই ভালো থাকার রহস্য ছিল তাদের বৈচিত্র্যময় খাবারের মেন্যু। আমাদের দেশে একজন কৃষক যেখানে সকালের নাশ্তায় ভাত খান, দুপুরের লাঞ্চে ভাত খান এবং রাতের ডিনারেও ভাত খান, সেখানে এই মানুষেরা সকালে হয়তো খেতো আঙুর আর মাশরুম, দুপুরে কচ্ছপের ফ্রাই আর রাতে খরগোশের স্টীক। পরের দিন আবার মেন্যু বদলে যেতো। এই করে করে সব রকম পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবারই তাদের খাওয়া হয়ে যেতো। পরবর্তীতে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ কোন একটা ফসলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এতে একে তো সব রকম পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার ছেড়ে এক শর্করার দিকে ঝুঁকে পড়ায় মানবজাতির সামগ্রিক স্বাস্থ্য আগের তুলনায় খারাপ হয়ে পড়ে, তার উপর এক বছর ধান না হলে পুরো দেশে দুর্ভিক্ষ লেগে যেতো। শিকারী সমাজ এই দিকে দিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। কোন একটা নির্দিষ্ট ফসলের উপর এদের নির্ভরশীলতা না থাকায় বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস—যাই হোক না কেন—এদের খাবার ম্যানেজ হয়ে যেত। আর কিছু না হোক, বার রকমের ফলমূল তো আছেই। আমাদের যাবতীয় রোগবালাইয়ের জন্মও এই ক্ষি সমাজে এসে। যতো রকম সংক্রামক রোগ আছে—হাম, যক্ষ্মা, বসন্ত—সব কিছুর জীবাণু আমাদের এই গবাদি পশু থেকে পাওয়া। আরেকটা কারণ এমন—কৃষি আর শিল্পভিত্তিক সমাজেই মানুষ অল্প জায়গায় অনেক মানুষ খুব ঘিঞ্জি পরিবেশে বাস করে। শিকারী সমাজে এর বালাই ছিল না। মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। কোন এক এলাকায় রোগের বিস্তার হলে সেই এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতো। মহামারী বিস্ত্ত হবার চান্সই পেত না। তাই বলে যে প্রাচীন মানুষের সব কিছুই যা ভালো ছিল—তা নয়।
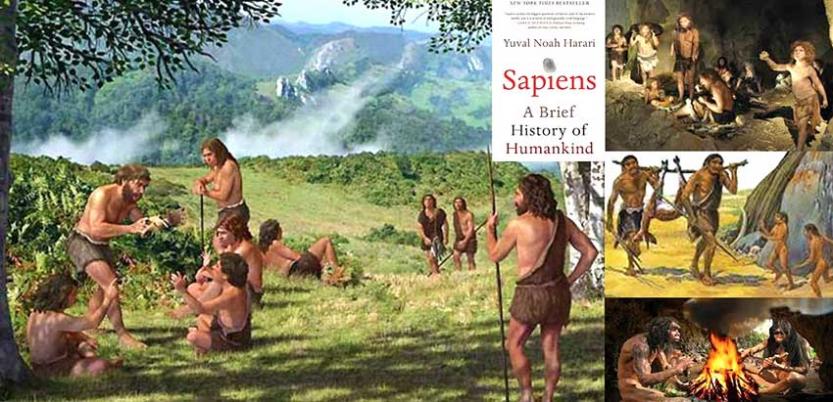
এই যে মহামারী বিস্ত্ত হবার চান্স পেত না, তার কারণ হচ্ছে সেই সমাজে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ফেলে সবাই অন্য কোথাও চলে যেত। বৃদ্ধদের অবস্থা তো ছিল আরো করুণ। বৃদ্ধ মাত্রই একটা দলের জন্য বোঝা। তো সেই বোঝা ঘাড় থেকে নামানোর জন্য তারা বৃদ্ধের কাঁধে কুড়োল দিয়ে আঘাত করে তাকে পরপারে পৌঁছে দিত। এই একটা দিকে আমরা আধুনিক মানুষ অনেক সভ্য হয়েছি বলা যায়। আমরা আমাদের বৃদ্ধ বাবা-মা কে কুড়োল দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলি না। বড়জোর বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে আসি। শিশু হত্যা তো ছিল অতি সাধারণ ঘটনা। অবশ্য শিশু হত্যার এই রেওয়াজ আমরা মধ্যযুগে আরবে আর তারও আগে গ্রীক সমাজে দেখেছি। শিশু জন্মগতভাবে দুর্বল বা ভগ্নস্বাস্থ্য হলে সেই শিশু সমাজের কোন কাজে আসবে না ভেবে তাকে হত্যা করতো। এই সেদিন পর্যন্ত প্যারাগুয়েতে আচে নামক এক জনগোষ্ঠী বাস করতো, যাদের জীবনধারা খুঁটিয়ে দেখলে প্রাচীন মানুষের জীবন আচরণের কিছুটা আঁচ পাওয়া যাবে। এরা এই আরব বা গ্রীকদের চেয়েও ছিল এক ধাপ এগিয়ে। শিশুর মাথায় চুল কম, তাকে মেরে ফেলো। শিশুটির চেহারা জোকার জোকার টাইপ—তাকে মেরে ফেলো। কিংবা দলে মেয়ে বেশি হয়ে গেছে। আর মেয়ের দরকার নাই। কাজেই, এই মেয়ে শিশুটিকে মেরে ফেলো। আমাদের ডেফিনিশন অনুযায়ী এগুলো হিংস্রতা। ওদের ডিকশনারীতে হয়তো এগুলোকে হিংস্রতা ধরা হত না। আমরা যেমন অবলীলায় মানবশিশুর ভ্রূণ মেরে ফেলি, ওরাও ঠিক তেমনি অদরকারি মানব শিশু মেরে ফেলতো। আফটার অল, মানুষ তো। কিছু নির্বিকার হিংস্রতা আমাদের রক্তে, ইতিহাসে বেশ ভালোভাবেই আছে। ফ্রান্সের দক্ষিণে লাসকাউ নামের এক গুহায় ১২ থেকে ২০ হাজার বছর আগে আঁকা ছবি পাওয়া গেছে। ছবিটায় একজন মরা মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। বাইসনের আক্রমণে যার ম্ত্যু হয়েছে। মানুষটির মুখে পাখির আদল। কেন—আমরা জানি না। মৃত্যুর পরও মানুষটির পুরুষাঙ্গ খাড়া হয়ে আছে। কেন—তাও আমরা জানি না। মানুষটির পাশেই আরেকটা পাখি দেখতে পাওয়া যায়, স্কলাররা বলেন—এই পাখি আমাদের আত্নার প্রতীক। বাইসনের আক্রমণে মানুষটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্নারূপী পাখিটি খাঁচা ছেড়ে পালিয়েছে। কথা হচ্ছে—-শিকারী মানুষেরা কি সত্যিই এতো গভীর অর্থ ভেবে ছবিটি এঁকেছিল? না এগুলো আমাদের ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেরপ্রিটেশনা? টাইম মেশিনে করে অতীতে যাওয়া ছাড়া এই রহস্য ভেদ করার আসলে কোন উপায় নেই। প্রায় ৯ হাজার বছর আগের ছবি পাওয়া গেছে আর্জেন্টিনার এক গুহায়। তখনো মানুষ শিকারী দশা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তবে মানুষ যে উন্নতি করছে—তার সমস্ত রকম লক্ষণ এই ছবিতে বিদ্যমান। এই ছবিকে বলা হয় শিকারী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই চিত্রকর্মের তাৎপর্যও আমরা সঠিক জানি না। আমি নিজে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম—পৃথিবীর মানুষ পাপে ডুবে আছে। এবং মানুষ সেটা জানেও। সমস্ত মানুষ এই পাপের গহবর থেকে মুক্তির জন্য হাত বাড়িয়েছে। আশা—কোন এক ঈশ্বর বা পয়গম্বর এসে তাদের এই অতল গহবর থেলে টেনে তুলবে। যথারীতি, আপনাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আর আর্টের মূল সৌন্দর্য তো এটাই। কোন ব্যাখ্যাই সঠিক না। আবার সব ব্যাখ্যাই সঠিক। এই চিত্রকর্মগুলো আসলে আমাদের এক অদেখা ভুবনে নিয়ে যায়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেমন ছিল, তাদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কার—এগুলো কেমন ছিল—তা বোঝার জন্য এই চিত্রকর্ম ছাড়া আমাদের হাতে খুব বেশি মালমশলা নেই। এই মালমশলাগুলো জোড়া লাগিয়েই আমরা আসলে আমাদের ইতিহাস নির্মাণ করি। ইতিহাসে তাই ধ্রুব সত্যি বলতে কিছু নেই। ইতিহাস আসলে আমাদের কল্পনার সবচেয়ে লজিক্যাল রূপায়ন। ওয়েল, চিত্রকর্ম ছাড়া আমাদের হাতে আর যা আছে, তা হল সেই আমলের কিছু ফসিল। বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলে পরিচয়! ঠিক তেমনি মানুষ তোমার কর্ম কী, ফসিলে পরিচয়। প্রত্নতাত্ব্বিকরা যেমন রাশিয়ায় তিরিশ হাজার বছর আগের এক কবর আবিষ্কার করেন। কবরটিতে তারা পঞ্চাশ বছর বয়স্ক এক লোকের কঙ্কাল পান যার সারা দেহ হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি মালা দিয়ে ঢাকা। হাতির দাঁত যে সেকালে বেশ দামী বস্তু ছিল, তা প্রাচীন ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন। সামান্য আইডিয়ার জন্য ‘রিভার গড’ পড়ে দেখতে পারেন। কিঞ্চিৎ মোটা বই। জীবন থেকে কয়েক ঘণ্টা মূল্যবান সময় চলে যাবে। কিন্তু আল্টিমেটলি ঠকবেন না—-কথা দিচ্ছি। লোকটার হাতে ছিল হাতির দাঁতের ব্রেসলেট। আশেপাশে আরো কিছু কবরে এরকম বাহারি মালার সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু ওগুলোতে পুঁতির সংখ্যা ছিল কম। এই থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ধারণা করেন—এই ব্যাটা নিশ্চয়ই দলের লীডার ছিল। এজন্যই তার কবরে হাতির দাঁতের ছড়াছড়ি। কে বলে প্রাচীন সমাজ সাম্যবাদী সমাজ ছিল! কেবল খাদ্যের দিক থেকে হয়তো ছিল। কিন্তু সামাজিক স্ট্যাটাস নির্ণয় করে যে উপাদানগুলো—সেদিক দিয়ে প্রাচীন সমাজ আজকের মতই বৈষম্য ও অনাচারে ভর্তি ছিল। তফাৎ এটুকুই —আমাদের সমাজে এই নির্ণায়কগুলো ফ্ল্যাট, গাড়ি-বাড়ি, তাদের সমাজে ছিল হাতের দাঁতের তৈরি গহনা।
অবশ্য এর চেয়েও বড় বিস্ময় প্রত্নতাত্ত্বিকদের জন্য এখানে অপেক্ষা করছিল। একটা কবরে তো দুটো কঙ্কালের খোঁজ পাওয়া গেলো। কঙ্কাল দুটো আবার উলটো দিকে করে মাথায় মাথায় লাগানো। একটা কঙ্কাল বার-তের বছর বয়সী একটা ছেলের। আরেকটা নয়-দশ বছর বয়সী একটা মেয়ের। প্রত্যেকের শরীরই হাতির দাঁতের তৈরি হাজার পাঁচেক পুঁতি দিয়ে ঢাকা। একটা পুঁতি নিখুঁতভাবে তৈরি করতে একজন শ্রমিকের পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগার কথা। সেই হিসেবে হাজার দশেক পুঁতি তৈরি করতে সাড়ে সাত হাজার শ্রমঘণ্টা লাগবে একজন শ্রমিকের। সোজা বাংলায় তিন বছরের মত। কার ঠেকা পড়সে তিন বছর খেটে এরকম মালা তৈরি করবে? আর ম্ত্যুর পর এরা নিশ্চয়ই মালা তৈরির জন্য তিন বছর অপেক্ষা করেনি। তার মানে একদল মানুষ মিলে অতি অল্প সময়ে এই গহনাগুলো তৈরি করেছে। এখন দলনেতাকে না হয় গহনা-টহনা পরিয়ে কবর দেয় যায়। এই বাচ্চাকাচ্চাকে কেনো? একদল বলেন, এরা সাধারণ বাচ্চাকাচ্চা না। এরা দলপতির সন্তান। কাজেই, এদের অকাল মৃত্যুতে দলপতি যে সম্মান পেত, এরাও সেই সম্মানই পাবে। ‘রিচ কিডস অফ ঢাকা’ রা যেমন পায় আরকি! আরেকদল বলেন, এদের সম্ভবত কোন রিচুয়ালের অংশ হিসেবে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হয়েছিল। কাজেই, এতো সম্মান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—মানুষ এই দেবতার আইডিয়া পেলো কোথ থেকে? এক কথায় এর উত্তর দেয়া সম্ভব না। তবে এটুকু অনেকটা নিশ্চিৎ, মানুষের মধ্যে প্রথম যে ধর্মের বিকাশ ঘটে—-তাকে বলা যায় এনিমিজন। এনিমিজম এর বাংলা হতে পারে প্রাণীপূজা। বেটার হয় আত্নাপূজা বললে। এরা বিশ্বাস করতো—সব কিছুর মধ্যেই আত্না বিরাজমান। সামান্য এই পাথর—সেই পাথরও চাইলে আমাদের জন্য দোয়া করতে পারে কিংবা আমাদের অভিশাপ দিতে পারে। খালি পাথরই নয়, বাড়ির পাশে যে পাকুড় বৃক্ষ কিম্বা বয়ে যাওয়া নদী—প্রত্যেকেরই আত্না আছে। মানুষ যে যুগ যুগ ধরে এদের পূজা করে আসছে—তা এই বিশ্বাস থেকেই। বস্তুজগতের সাথে মানুষের এই যে আত্নার সম্পর্ক—এটা কিন্তু নতুন নয়। বহুদিন একটা মোবাইল সেট ব্যবহার করে দেখবেন, ঐ সেটটার প্রতি মায়া পড়ে যাবে। বাজারে নতুন স্মার্টফোন এলেও সেটা তখন আর ফেলে দিতে ইচ্ছা হবে না। যারা ঋত্বিকের (ঋত্বিক রোশন না, ঋত্বিক ঘটক) ‘অযান্ত্রিক’ দেখেছেন, তারা ব্যাপারটা আরো ভালো রিলেট করতে পারবেন। গল্পে নায়কের পেটে ভাত নেই, কিন্তু সে তার প্রিয় গাড়িটা তবু বেঁচবে না। সে গভীরভাবে বিশ্বাস করে, গাড়িটার একটা প্রাণ আছে। আত্না আছে। গাড়িটা বেঁচে দিলে সে নিজে যেমন প্রেমিকা হারানোর ব্যথায় কষ্ট পাবে, গাড়িটাও কম দুঃখ পাবে না। এনিমিস্টরা বিশ্বাস করে—মানুষ আর তার আশেপাশের সত্তার মধ্যে কোন ব্যবধান নেই, কোন হায়ারার্কি নেই। মানুষের জন্য সবাই, আবার সবার জন্য মানুষ।
একজন শিকারী যেমন নাচ-গান সেরেমনির মাধ্যমে একদল হরিণকে তাদের ডেরায় ইনভাইট করতে পারে। তারপর তাদের রিকোয়স্ট করতে পারে—হরিণের দলের একজন যেন স্বেচ্ছায় আত্নউৎসর্গ করে। তাদের বিশ্বাস ছিল, ঠিকমত মেসেজ দিতে পারলে হরিণের কাছেও মেসেজ পৌঁছানো সম্ভব। হরিণ যদি নিজে থেকেই নিজেকে কুরবানী করে তো ভালো, না হলে হরিণ শিকার করে পরে মাফটাফ চেয়ে নিলেই হবে। এইখান থেকেই সম্ভবত ধারণা আসে যে, হরিণের কাছে মেসেজ পৌঁছানো গেলে মৃত আত্নার কাছে পৌঁছানো যাবে না কেন? এইখান থেকেই প্রাচীন সমাজে শামানের উৎপত্তি। শামানদের কাজ ছিল এই জগতের মানুষের সাথে অন্য জগতের মানুষের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া। এই অন্য জগৎ মানে নট নেসেসারিলি পরজগৎ। অনন্ত অসীম পরজগত কিংবা একক ঈশ্বরের ধারণা তখনো গড়ে ওঠেনি। কিন্তু মানুষ মরে গেলেও যে তার আত্না মরে না আর সেই আত্না জীবিতাবস্থায় তার কাছের মানুষদের আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়, তাদের ভালো করে কিংবা অনিষ্ট করে—এই ব্যাপারে তাদের একটা পাকাপাকি রকম বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। অবশ্য আবারও ঐ একই কথা। পুরোপুরি নিশ্চিত করে আমরা কিছুই বলতে পারি না। অতীতকে ডিকোড করার জন্য আমাদের হাতে যে সামান্য কিছু চিত্রকর্ম আর ফসিল ছাড়া তেমন কিছু নেই। বলা হয়, আমরা সবাই কাবিলের সন্তান। বড় ভাই কাবিল ছোট ভাই হাবিলকে খুন করে পৃথিবীতে তার লিগ্যাসী প্রতিষ্ঠা করে গেছে। কাজেই, অল্পবিস্তর খুনে সত্তা আমাদের সবার মধ্যেই কমবেশি আছে। কারোটা প্রকাশ্য, কারোটা শিক্ষা-সংস্ক্তির মোড়কে এখনো ঢাকা পড়ে আছে। এই হাবিল-কাবিলের যে গল্পটা আমরা ছোটবেলায় শুনেছি, তাতে কিছুটা ফাঁকি আছে। হাবিল ভালো আর কাবিল খারাপ —এই বাইনারীর ছাঁচে পুরো ঘটনা ফেলতে গিয়ে মূল বিষয়টাই আমাদের স্পর্শ করা হয় না। কেননা প্থিবীর বাকি অর্ধেক গল্পের মতই এই গল্পের মূলেও আছে সেক্স। হাবিল-কাবিল দুই ভাই। এতোদূর পর্যন্ত গল্পটা ঠিকঠাক এগোয়। সমস্যাটা হয় তখনই, যখন হাবিলের সাথে তার এক যমজ বোনের জন্ম হয়। আর কাবিলের সাথে জন্ম নেয় আরেক যমজ বোন। এখন হাবিল-কাবিল হচ্ছে আদমের দুই সন্তান। পৃথিবীতে তখন মানুষ বা জনপ্রানী বলতে আর কেউ নেই। কাজেই, মানবজাতির বংশরক্ষার জন্য আপন বোনকে বিয়ে করা ছাড়া আর কোন গতি ছিল না। আল্লাহ তখন একটা নিয়ম করে দিলেন। হাবিল বিয়ে করবে কাবিলের সাথে জন্ম নেয়া যমজ বোনকে। কাবিলের ক্ষেত্রে সেটা ভাইস ভার্সা। এখন দেখা দিল আসল সমস্যা। কাবিলের সাথে জন্ম নেয়া যমজ বোনটা বেশি সুন্দরী। কাবিল তাকেই বিয়ে করতে চায়। এদিকে হাবিল আল্লাহর আদেশের ভয়েই হোক কিংবা কাবিলের যমজের সৌন্দর্যে আক্ষ্ট হয়েই হোক—সেও তাকেই বিয়ে করতে চায়। হাবিলের সাথে জন্ম নেয়া যমজটার ওদিকে কোন খবর নেই। সে সুন্দরী নয় বলে কেউ তাকে পাত্তা দেয় না। কাজেই, সুন্দরী মেয়েরা সামান্য ভাব নিলেও এতে রাগ করার কিছু নেই। সৃষ্টির শুরু থেকেই এমনটা চলে আসছে। যাই হোক, আদম তখন তাদের একটা প্রস্তাব দিলেন। দু’জনকে বললেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কিছু একটা কুরবানী দিতে। যার কুরবানীতে আল্লাহ লাইক দিবেন, সেই কাবিলের যমজ বোনকে পাবে। কাবিল কিছু শস্য অফার করলো আল্লাহকে। আর হাবিল দিল একটা সুস্থ সবল ছাগল। বলা বাহুল্য, হাবিলের কুরবানী কবুল হল। কাবিল মনে করলো, এই সব তার বাপের কারসাজী। হাবিল তার বাপ আদমের পছন্দের ছেলে বলে আদম তার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করেছে। বাকি ইতিহাস আমাদের জানা। কাবিল হাবিলকে মেরে ফেললো। এইখানেই গল্প শেষ নয়। মেরে ফেলার পর সে বিরাট অনুতপ্ত হল। আর হাবিলের লাশ নিয়ে পথে পথে ঘুরতে থাকলো। হাবিল-কাবিলের এই মিথ যে কেবল আব্রাহামিক কালচারেই সীমাবদ্ধ—তা নয়। রোম নগরীর প্রতিষ্ঠার পেছনেও এমন একটা মিথ চালু আছে। দুই ভাইয়ের যুদ্ধ ও রক্ত থেকে রোম নগরীর পত্তন। একই মিথ সম্ভবত এক এক জায়গায় এক একভাবে ছড়িয়েছে। আসল কথা, মানবজাতির ভায়োলেন্সের ইতিহাস খুব নতুন কিছু নয়। বাস্তবে ভায়োলেন্স ছিল বলেই মিথে সেটা বারবার এসেছে। কাজেই, মিথ ছেড়ে এবার বাস্তবে আসি। পর্তুগালে একটা প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ করে দেখা গেলো, ৪০০ কঙ্কালের মধ্যে মাত্র দুটোতে ভায়োলেন্সের চিহ্ন পাওয়া গেছে। একই রকম ফলাফল পাওয়া গেছে ইসরায়েলেও।
এখানে ৪০০ কঙ্কালের মধ্যে মাত্র একটিতে ভায়োলেন্সের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই ফলাফলগুলো মানুষের হিংস্রতার সপক্ষে খুব জোরালো প্রমাণ নয়। ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট পাওয়া গেছে দানিউব উপত্যকায়। এখানে ৪০০ কংকালের ১৮টিতে ভায়োলেন্সের প্রমাণ স্পষ্ট। শুনে সংখ্যাটা কম মনে হতে পারে। কিন্তু পার্সেন্টেজ করলে ব্যাপারটার ভয়াবহতা বোঝা যাবে। জরিপের ফলাফলকে সঠিক ধরলে বলতে হয়, শতকরা ৪.৫ ভাগ মানুষ সে উপত্যকায় মারামারি খুনোখুনি করে মরতো। আজ এই পার্সেন্টেজ নেমে এসেছে ১.৫ এ। সমস্ত যুদ্ধ, টেরোরিস্ট এ্যাটাক আর লোকাল সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাস মিলিয়েই। তাইলেই বোঝেন, দানিয়ুব উপত্যকার মানুষ সেকালে কীরকম হিংস্র ছিল। এর সাথে কেবল তুলনা দেয়া যায় বিশ শতকের হিংস্রতার। লিখিত ইতিহাসে মানবজাতি সবচেয়ে বাজে সময় পার করেছে বিশ শতকে।
ও দুটো বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের। ফলাফল—বিশ শতকে প্রতি ১০০ জনে ৫ জন ভায়োলেন্সে মরেছে। হাবিল-কাবিলের গল্প বড়জোর ৬ হাজার বছর পুরানো। সুদানেই ১২ হাজার বছর আগের এক কবরস্থানে ৫৯টা এমন কঙ্কাল পাওয়া গেছে যার মধ্যে ২৪টার গায়েই তীরের ফলার চিহ্ন পাওয়া গেছে। এক মহিলার গায়ে তো রীতিমত ১২টা ক্ষতচিহ্ন। যুদ্ধ শেষে পরাজিত গোত্রের নারীদের সাথে কী ব্যবহার করা হয়—আমরা সবাই জানি। এই কালচার হঠাৎ মধ্যযুগে তৈরি হয়নি। বহু আগে থেকেই এই নেশা আমাদের রক্তে মিশে আছে। ব্যাভারিয়া (আজকের জার্মানিতে) জাস্ট একটা কবরের মধ্যেই খালি নারী ও শিশুদের লাশ পাওয়া গেছে। কোনরকম যত্ন ছাড়াই স্তূপ করে রাখা লাশ। প্রতিটা লাশই সেকালের অস্ত্র দিয়ে ভয়ানক রকম খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা। অল্প যে ক’টা পুরুষ কঙ্কাল পাওয়া গেছে, প্রতিটাতেই অত্যাচারের চিহ্ন আরো ভয়াবহ। বোঝাই যায়, কোন এক গোত্রের উপর সেসময় গণহত্যা হয়েছে। হত্যা শেষে সবগুলো লাশ নির্মমভাবে এক কবরে চাপা দেয়া হয়েছে। এর সাথে কেবল তুলনা চলে নাৎসী জার্মানদের কিংবা ৭১ সালে পাকিস্তানিদের বর্বরতার। আমাদের হাতে এভিডেন্স আসলে খুব কম। কাজেই আমরা নিশ্চিৎ করে বলতে পারছি না অধিকাংশ মানুষ পর্তুগাল আর ইসরায়েলের সেকালের অধিবাসীদের মত শান্তশিষ্ট ছিল না দানিউব উপত্যকার মত খুনে, রক্তলোলুপ ছিল। তবে সেকালের দানিয়ুব বা সুদানের তুলনায় কিংবা এই তো সেদিনের বিশ শতকের তুলনায় আমরা যে এখনো অনেক ভালো আছি—একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। শতাব্দীর শেষাবধি এই কনসিস্টেন্সি ধরে রাখতে পারি কিনা—সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন?
তথ্যঃ মনুষ্যজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থ
লেখক - ইউভাল নোয়া হারারি
ভাবানুবাদ : আশফাক আহমেদ
বিশেষ কৃতজ্ঞতা : কাজান চৌধুরী
About Writer :
Prof. Yuval Noah Harari is a historian, philosopher, and the bestselling author of Sapiens: A Brief History of Humankind, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, 21 Lessons for the 21st Century, and the series Sapiens: A Graphic History and Unstoppable Us. His books have sold 45 Million copies in 65 languages, and he is considered one of the world’s most influential public intellectuals today. Born in Israel in 1976, Harari received his PhD from the University of Oxford in 2002 and is currently a lecturer at the Department of History at the Hebrew University of Jerusalem. (Wikipedia)
ই:স:/জ:নি:/২৮-০৮-২০২৩
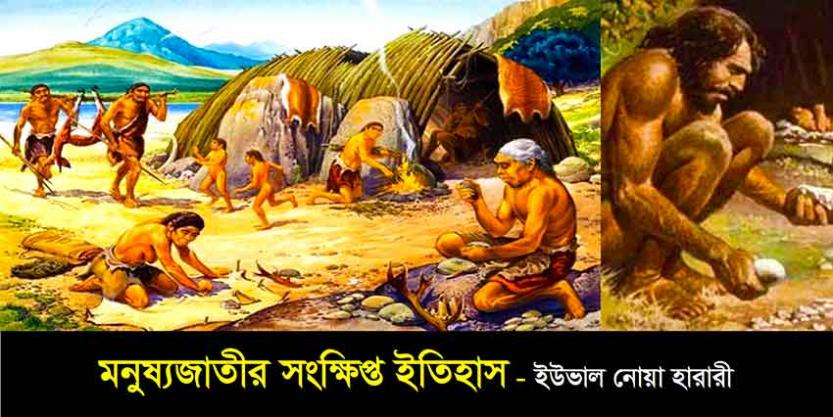
পাঠকের মন্তব্য